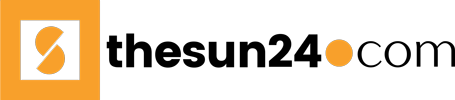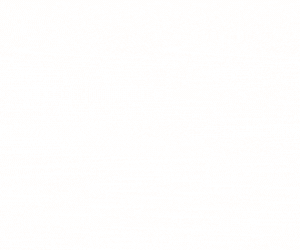দেশব্যাপী বিক্ষোভের মুখে গত আগাস্টে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে যেমন রয়েছেন তার সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, তেমনি ছিলেন নাগরিক সমাজের কর্মী এবং সেইসঙ্গে উগ্র ইসলামপন্থীদের একটি বিস্তৃত জোট। শেখ হাসিনার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব সামাজিক আন্দোলনে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।
হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বিভিন্ন আদর্শিক ধারার বাংলাদেশিরা নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হন, যিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান হিসেবে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যে আশা নিয়ে ইউনূসকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, বিশেষকরে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলা ও সামাজিক অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার যে স্বপ্ন অনেকে দেখেছিলেন, তা এখন অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ। তার পররাষ্ট্রনীতি এবং তার আমলে বিভিন্ন শক্তি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় ইউনূস সরকারের প্রতি জনআকঙ্ক্ষা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, দেশের ভবিষ্যত নিয়েও তাই অনেকে শঙ্কিত।
অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ইসলামপন্থীদের লাগাম টেনে ধরতে অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিবেশি ভারতের সাথে থাকা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে সরে এসে চীন ও পাকিস্তানকে কাছে টানতেই বেশি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনই বাংলাদেশ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য তৈরি করতে পারে প্রতিকূলতা।
১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়ও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে বাঙালির ভাষাগত জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশিরা তাদের ভাষাগত ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত এবং তারা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে।
তা যাই হোক, এই ভাষাগত ঐতিহ্য বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে অস্বস্তিকরভাবে সহাবস্থান করেছে: আর তা হলো কট্টর ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার, যা আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ এই পরিচয়ের মূলেই মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা। পশ্চিমবঙ্গে অধিবাসীরা বাংলা ভাষাভাষী হলেও ধর্মীয় কারণে দুই দেশের মধ্যে একটি বিভেদ রেখা রয়েছে।
বাংলাদেশের প্রতি ইসলামাবাদের আসক্তি ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক উভয় উৎস থেকেই উদ্ভূত। যখন বাংলাদেশ একটি অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ ছিল, তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল কট্টর সুন্নি ইসলামী নীতির প্রতি আনুগত্য। এবং একটি উগ্র ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামী, যারা কি না স্বাধীনতা-পূর্ব এবং পরবর্তী উভয় বাংলাদেশেই একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে টিকে আছে, যদিও এর উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী প্রভাব নেই।
১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য স্বাধীনতার সপক্ষের বাংলাদেশিদের কাছে জামায়াতে ইসলামী রীতিমতো ঘৃণার পাত্র। কারণ এর সদস্যরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস অভিযানের পক্ষে ছিলেন। তবে এ-ও সত্য বাংলাদেশিদের একটি অংশ এখনও জামায়াতে ইসলামীর প্রতি সহানুভূতিশীল। এর কারণ ধর্মবিশ্বাস।
সম্প্রতি, জামায়াতে ইসলামী এবং এর অনুসারীরা পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে সমর্থন পেতে শুরু করেছে। এই দেশগুলো থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে তহবিলের পাশাপাশি ওই অঞ্চলের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদর্শিক দীক্ষাও নিয়ে এসেছেন তারা। আর এই আর্থিক সামর্থ্য ও আদর্শিক দীক্ষা বাংলাদেশের জটিল ঐতিহাসিক শিকড় ও ইসলামের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে ক্রমাগতভাবে ক্ষুণ্ন করছে।
এটি সত্য, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক কারণে হাসিনা তার শাসনামলে জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দেশে, তাকে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটের প্রতি নজর রাখতে হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বিষয়টি ভারতও বেশ ভালোভাবে গ্রহণ করেছিল। দেশজুড়ে সহিংসতা ও বিক্ষোভ উসকে দেওয়ার জেরে সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির কিছুক্ষণ আগে হাসিনার সরকার জামায়াতে ইসলামী ও এর ছাত্র সংগঠনকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
তবে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ইউনূস জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আরও সহনশীল মনোভাব প্রদর্শন করে আসছেন, যার মধ্যে হাসিনার আমলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ইসলামী শক্তিগুলোর মুখোমুখি না হওয়ায়, তারা দিনকে দিন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, হিন্দু সংখ্যালঘু ছাড়াও আহমদিয়া সম্প্রদায় তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশের এই ঘটনাপ্রবাহের ফলে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরও বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমণ ভারতের মুসলমানদের প্রতি বৈরীতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে, যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।
এই ধরনের পাল্টা সহিংসতার ঘটনা অতীতের দিকে তাকালেও বেশ চোখে পড়ে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে, হিন্দু উগ্রপন্থীরা যখন ভারতের উত্তর প্রদেশে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করলো তখন বাংলাদেশেও হিন্দু সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে ব্যাপক হারে হামলা হয়েছিল। প্রখ্যাত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন তার লজ্জা উপন্যাসে ওই ঘটনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।
ইসলামপন্থী উগ্রবাদের প্রতি ইউনূস সরকারের দরদ উত্তর-পূর্ব ভারতে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা এবং সহিংসতাকে আরও উসকে দিতে পারে, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে দেখা দিতে পারে অস্থিতিশীলতা। তাছাড়া বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিশ্চিতভাবে হিন্দুদের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করবে।
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ঢাকা ও নয়া দিল্লির দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক। যদিও ইউনূস সম্প্রতি ভারতের দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির পথে হাঁটছেন। মার্চের শেষের দিকে বেইজিং সফরে মুহাম্মদ ইউনূস দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য বাংলাদেশকে সম্ভাব্য পাদদেশ হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য স্থলবেষ্টিত হওয়ায় কেবল বাংলাদেশই চীনকে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার দিতে পারে। ঢাকাকে ‘সমুদ্র প্রবেশাধিকারের অভিভাবক’ হিসেবেও উল্লেখ করেছিলেন তিনি।
যদিও চীন এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি, তবে ইউনূসের মন্তব্য ভারতের কূটনৈতিক এবং পররাষ্ট্র মহলে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। কারণ বঙ্গোপসাগরে বন্দরগুলোতে চীনের প্রবেশাধিকার ভারতের সমুদ্র নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মূল্য দিতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কা উল্লেখযোগ্য চীনা বিনিয়োগ চাওয়ার পর কিছু বিশ্লেষক একে ‘ঋণের ফাঁদ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।
উভয় ঘটনাই ভারতের জন্য নেতিবাচক, যাদের বাংলাদেশ বিষয়ে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখা উচিত। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে চীন দীর্ঘদিন ধরে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক উপভোগ করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নেপাল এবং শ্রীলঙ্কায়র দিকেও হাত বাড়িয়েছে তারা। আংশিকভাবে বেইজিং তার অবস্থান প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ নয়াদিল্লি তার প্রতিবেশীদের উদ্বেগ মোকাবেলায় কোনো সুসংগত নীতিমালা তৈরি করতে পারেনি।
যদি বাংলাদেশ সত্যিই ইসলামপন্থীদের অধীনে চলে যায় এবং সক্রিয়ভাবে চীনের কক্ষপথে চলে যেতে শুরু করে, তাহলে ভারত নিজেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে পাবে এবং তার সীমান্ত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে বাধ্য। আরও খারাপ বিষয় হল, নয়াদিল্লি সম্ভবত একটি অমূল্য অংশীদার হারাবে, যার জন্য তারা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগও করেছে।
এই দুই উদীয়মান প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ভারতের কূটনীতিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। নয়া দিল্লি সম্ভবত ঢাকায় তার প্রভাবের ক্রমাগত ক্ষয় দেখতে পারছে না। রাজনীতির পরিবর্তন বা চীনের সাথে ইউনূস সরকারের প্রেমের বিষয়ে কেবল সতর্ক করার পরিবর্তে, ভারতকে নিজস্ব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতি তার দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন তুলে ধরা, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং ভারতের বাজারে প্রবেশাধিকার নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে তা নিয়ে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ জরুরি। অন্যথায়, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতির ঝুঁকি বাস্তব রূপ পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।
সুমিত গাঙ্গুলি: কলামিস্ট, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হোভার ইনস্টিটিউশনের সিনিয়র ফেলো।
ইংরেজি থেকে অনূদিত