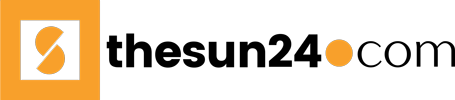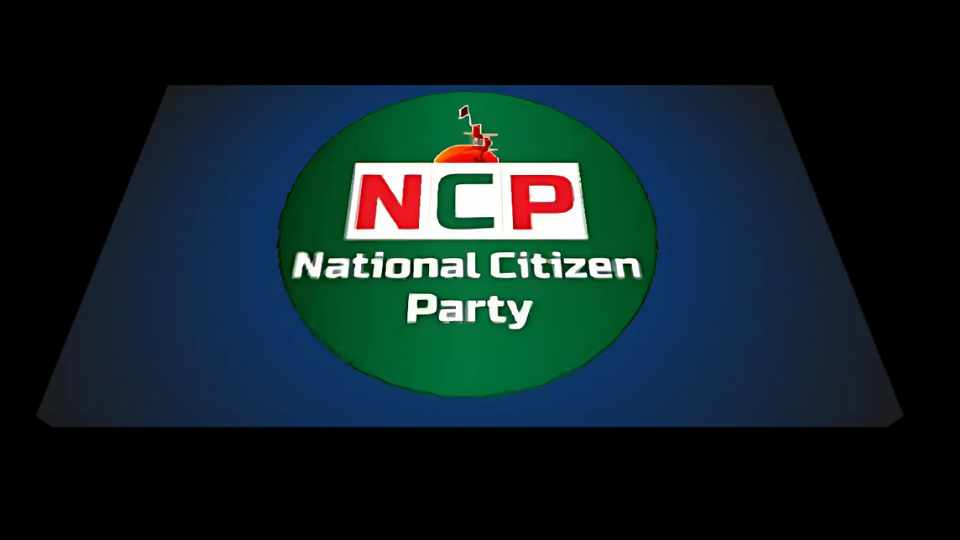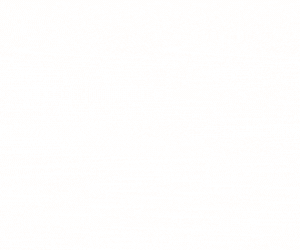রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই মাসের শুরুতে বিভিন্ন দেশের নেতাদের ধন্যবাদ জানান। এসময় তিনি দীর্ঘদিনের মিত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ দেন তার ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের পক্ষের অবস্থানের জন্য।
পুতিনের ওই ফোনকলের বিষয়টি ভারতীয় মিডিয়াতে বেশ ফলাও করে যেমন প্রচার করা হয়েছিল, তেমনি সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় নেটিজেনদের বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছিল ঘটনাটি।
এর অবশ্য কারণও আছে। অন্য অনেক দেশের চেয়ে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে ভারতের পদক্ষেপ ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধে মোদীকে একাধিকবার বৈশ্বিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা গেছে।
আর এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে— ভারত কেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসনে আরও সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করছে না?

এমন প্রশ্ন ওঠার একটি বড় কারণ অতীতে ভারতের নেওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করে একটি নতুন দেশের জন্মে সহায়তা করেছে ভারত। ১৯৮৮ সালে মালদ্বীপে সশস্ত্র ভাড়াটে সেনাদের হামলা প্রতিহত করে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করেছে। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে সহায়তা করেছে। সম্প্রতি ভারত সমুদ্র এলাকায় জলদস্যুতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।
বিশ্বকল্যাণে ভারতের স্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় ‘ভ্যাকসিন মৈত্রী’ উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত অনেক দেশে টিকা সরবরাহ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভারত কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোট গঠন করেছে। এছাড়া ভারত বিশ্বের সঙ্গে ডিজিটাল অবকাঠামো ভাগ করে নিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও ভারত প্রথম সহায়তা দানকারী হিসেবে কাজ করেছে।
গত দুই দশকে ভারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স উভয় সরকারই এ লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর ফলে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থানে পৌঁছে ভারত মনে করেছে, আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক সংঘাতে সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নিলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
কূটনীতিকরা মনে করেন, ভারতের এই সতর্ক অবস্থান কিছু কারণে হতে পারে। ভারত মনে করতে পারে, আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার ভারতের ধারণা থাকতে পারে, এসব সংঘাত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। যেমন, পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু দেশটি উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে বেশি সক্রিয় হতে চায় না। কারণ ওই রাষ্ট্রগুলোই গাজা ও ওই অঞ্চলের সংকটের প্রতি সীমিত মনোযোগ দিচ্ছে।
তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, বৈশ্বিক শৃঙ্খলার দুর্বলতার মাঝে ভারত বৈশ্বিক নেতৃত্বের দিকে এগোতে পারে। আর এজন্য ভারতের ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। এটি ভারতের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের জন্য বাধা হবে না, বরং সহায়ক হবে।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ভারত নিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়া দেশগুলোকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। একইভাবে, বর্তমান বিশ্বের জটিল পরিস্থিতিতে বহুমুখী সম্পর্ক নীতি গ্রহণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এর মাধ্যমে ভারত প্রতিটি প্রধান দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করছে।
তবে পার্থক্য হলো— নিরপেক্ষ নীতি ছিল গ্লোবাল সাউথের জন্য। আর বহুমুখী সম্পর্ক নীতি মূলত ভারতের নিজস্ব স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে।
অবশ্য একটি দেশ যখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠে, শক্তিশালী গণতন্ত্র হিসেবে গর্ব করে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশাও বেড়ে যায়।

ভারতের শুধু অবস্থান নেওয়া বা দর্শকের ভূমিকা পালন করা যথেষ্ট নয়। ভারত যদি নিরাপত্তা পরিষদে বলে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে একই যুক্তি পরিষদের বাইরে নেওয়া সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
প্রেসিডেন্ট পুতিনের বক্তব্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া সফর করে মোদী সাহসী অবস্থান নিয়েছিলেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে ভারত নিরপেক্ষ থেকেছে, যদিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ ছিল। এতে অন্যান্য বড় উন্নয়নশীল দেশও যুদ্ধ নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিতে উৎসাহিত হয়েছে।
এছাড়া মোদী আগে থেকেই পুতিনকে বলেছিলেন, এটি ‘যুদ্ধের যুগ নয়’ এবং পরামর্শ দিয়েছেন যেন রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করে। তবে পুতিনের সাম্প্রতিক মন্তব্য ভারতের জন্য বড় ভূমিকা নেওয়ার এক সূক্ষ্ম আহ্বানও হতে পারে। ভারতই অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য দেশ, যা রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাহলে, ভারত কি এই সঙ্কট নিরসনে বড় ভূমিকা রাখার উপযুক্ত নয়?
ভারত এই প্রত্যাশা পূরণ না করলে তুরস্ক, সৌদি আরব বা কাতারের মতো দেশগুলোর জন্য সুযোগ তৈরি হবে। তারা ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ চীন সাগরের সংঘাত নিরসনে ভূমিকা রাখবে, যেখানে ভারতের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ।
২০২২ সালে ইউক্রেন ও রাশিয়ার বৈঠক তুরস্কে হয়েছিল। সম্প্রতি, সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেনের আলোচনা হয়েছে। এটি সৌদি আরবের বহুমুখী কূটনৈতিক নীতিরই অংশ। রুয়ান্ডা ও কঙ্গোর রাষ্ট্রপতিরাও কাতারে বৈঠক করেছেন পূর্ব কঙ্গোতে যুদ্ধবিরতি আনতে।
জাতিসংঘে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি টি.এস. তিরুমূর্তির মতে, ভূরাজনৈতিক প্রভাবের গুরুত্ব ট্রাম্প প্রশাসনও বোঝে। অথচ অতীতে আফগানিস্তান বিষয়ে ট্রোইকা প্লাস বৈঠকে বা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উপেক্ষা করেছিল, যদিও ভারত তাদের কৌশলগত অংশীদার।
বিশ্ব এখন নতুন এক পরিবর্তনের মুখে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু অংশ ডানপন্থী নীতির দিকে ঝুঁকছে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও এশিয়ায় তার সম্পৃক্ততা কমাতে পারে। পাশাপাশি বাণিজ্যে বিভাজন ও রক্ষণশীল নীতি বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতকে শুধু নিজের অবস্থান রক্ষার চেয়ে বৈশ্বিকভাবে আরও সক্রিয় হতে হবে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।
ভারতের সঙ্গে চীনের বৈরী সম্পর্ক দ্রুত শেষ হবে না। এছাড়া সরবরাহ ব্যবস্থার সংযুক্তির কারণে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি আরও বাড়তে পারে। তাই আঞ্চলিক সীমার বাইরে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা জরুরি ভারতের জন্য।
এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছে অঞ্চলগুলোকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে বিভক্ত করতে পারে। এতে এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে পারে। আর এমন হলে কোয়াড (ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র) তার কৌশলগত গুরুত্ব হারাতে পারে এবং ভারত চাপে পড়তে পারে।
আর এই কারণেই ভারতের এখন আঞ্চলিক নীতির দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশি বলেও মনে করেন অনেকে। কারণ আঞ্চলিক নীতি শুধু ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সমষ্টি নয়, যেমন পশ্চিম এশিয়া বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনে তার অংশগ্রহণ কমিয়ে দিয়েছে।
পূর্ব এশিয়া ভারতের বাড়তি মনোযোগ দাবি করে। বিশেষত রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) থেকে ভারতের সরে আসার পর। এটি ইউরোপের প্রতি কৌশলগত মনোযোগের সময়। কারণ সেখানে চাপ বাড়ছে।
এছাড়া ভারতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত প্রত্যাশা পূরণের জন্য অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্কারের সময়ও এখন। এই চুক্তি ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আরও ব্যাপক সম্পর্কের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে।
তবে সংঘাতের মধ্যে সক্রিয় থাকা মানে এই নয় যে ভারত মধ্যস্থতাকারী হবে বা এক পক্ষ থেকে অন্যপক্ষে বার্তা পাঠাবে। এছাড়া যুদ্ধরত পক্ষগুলো বা কোনো প্রভাবশালী শক্তি যেমন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আমন্ত্রণ জানাবে কি না তা নিয়ে অপেক্ষা করা একটি বুদ্ধিমান নীতি হতে পারে। তবে তারা ভারতকে আমন্ত্রণ জানাবে না, যতক্ষণ না নয়াদিল্লি তার ভূরাজনৈতিক ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট না করে।

১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ান যুদ্ধের সময় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নয়। ভারত তখন মাত্র চার বছর স্বাধীন হয়েছিল এবং এটি একটি দারিদ্র্যগ্রস্ত দেশ ছিল। তবুও এটি পিছিয়ে যায়নি। তার এই ভূমিকার জন্য ভারতকে নিরপেক্ষ দেশগুলোর প্রত্যাবাসন কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল।
সম্প্রতি ২০২১-২২ সালে ভারত যখন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল, তখন দেশটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেতুবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল।
জাতিসংঘে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি টি.এস. তিরুমূর্তির মতে, বর্তমান ট্রাম্পময় বিশ্বের শৃঙ্খলা বড় শক্তিগুলোর পক্ষেই গড়ে উঠছে এবং ভূরাজনৈতিক বিভাজন ও একতরফা নীতির প্রসার ঘটছে। এমন অবস্থায় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনীতি একে অপর থেকে আলাদা মনে করা উচিত নয়। পূর্ণ সুবিধা লাভের জন্য দেশটিকে বহুমুখী সম্পর্ক নীতি প্রয়োগ করতে হবে। ভারতকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের সুযোগ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে হবে। পাশপাশি ভেঙে পড়া বিশ্ব শৃঙ্খলা নতুন করে গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
তথ্যসূত্র : দ্য হিন্দু।