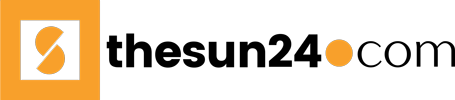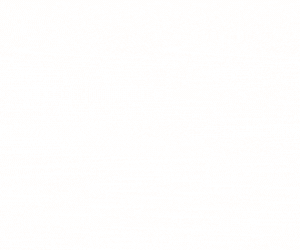তুমুল আলোচনা এখন বর্ষবরণের শোভাযাত্রার ‘ফ্যাসিবাদের’ মুখাকৃতি নিয়ে; এটি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখনই উঠছিল আলোচনা। কেননা এর সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেহারার স্পষ্ট মিল পাওয়া যাচ্ছিল।
পহেলা বৈশাখের দুদিন আগে এক দুষ্কৃতী চারুকলায় ঢুকে সেই মোটিফটি পুড়িয়ে দেয়। তারপর এক দিনের চেষ্টায় তড়িঘড়ি করে নতুন মোটিফ তৈরি হয়, যা নিয়ে সোমবার বের হয় ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’। শিং, রক্তমাখা মুখের এই মোটিফেও শেখ হাসিনার সঙ্গে মিল যাওয়া যাচ্ছে।
এক পক্ষ অভিযোগ তুলেছে, ক্ষমতার পালাবদলে বর্ষবরণের এই আয়োজন রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। তার জবাব দিতে গিয়ে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেছেন, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।
অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে বর্ববরণের আয়োজনই শুরুই হয়েছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে।
এই শোভাযাত্রার নাম মঙ্গল শোভাযাত্রা থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা করা পেছনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলে দাবি করছেন এখনকার আয়োজকরা।
এর বিপরীতে যুক্তি হিসাবে অনেকে দেখাচ্ছেন মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে ইসলামী সংগঠনগেুলোর আপত্তি তোলার কথা। এর নাম মঙ্গল শোভাযাত্রা থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা করতে হেফাজতে ইসলামের সম্প্রতি দাবি তোলার কথা। ফলে এখানেও আসে রাজনীতি।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে দুটি আয়োজন, দুটিই রাজনৈতিক আন্দোলন ধারণ করে আছে।
পাকিস্তান আমলে গত শতকের ষাটের দশকে বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার দিশা দিয়েছিল ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। তার দুই দশক পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা।
এইচ এম এরশাদের শাসনকালে ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আনন্দ শোভাযাত্রা নামে এই আয়োজনের শুরু। তারপর এটি মঙ্গল শোভাযাত্রা নাম নেয়। এই নাসেই জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কোর বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়।
চারুকলার শিক্ষক নিসার হোসেন বলেন, “তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছিল। তার বিপরীতে সব ধর্মের মানুষের জন্য বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে। তারাই মূলত এই আয়োজনটি করেছিল। এই শোভাযাত্রা তখন থেকেই স্বৈরাচারবিরোধী এবং মৌলবাদবিরোধী।”
তারপর সমা্জ ও রাজনীতির দাবি মিটিয়েই যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হচ্ছে, তা প্রতিবারের প্রতিপাদ্য দেখলেই স্পষ্ট হয়।
২০১৩ সালে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিক্রিয়া দেখানো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধের ডাক ছিল মঙ্গল শোভাযাত্রার স্লোগানে; সেবার প্রতিপাদ্য ছিল- ‘রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ অনিঃশেষ’।
পরের বছরের প্রতিপাদ্য ছিল- ‘উদ্যত কর, জাগ্রত কর, নির্ভয় কর হে’। ২০১৫ সালে উগ্রপন্থিদের হাতে লেখক-অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট খুনের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য ছিল- ‘অনেক আলো জ্বালতে হবে মনের অন্ধকারে’।
এভাবে ২০১৬ সালে শিশু নির্যাতনের ঘটনার প্রেক্ষাপটে শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল- ‘অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে‘। ২০২১ সালে কোভিড মহামারির মধ্যে সীমিত আয়োজনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘কাল ভয়ংকরে বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর’। গত বছর অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৪৩১ বরণে প্রতিপাদ্য ছিল- ‘আমরা তো তিমিরবিনাশী’।
গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এবার মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাম বদলে আনন্দ শোভাযাত্রা করে। তার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, শুরুর নামটিতে ফেরত গেছেন তারা।
তবে নিসার হোসেন বলছেন, শুরুতে মঙ্গল শোভাযাত্রা নামই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এর ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, এই ভেবে আনুষ্ঠানিকভাবে নামটি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে তা মঙ্গল শোভাযাত্রা নামেই পরিচিতি পায়।
এবার শোভাযাত্রায় ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতির পাশাপাশি জুলাই অভ্যুত্থানের মোটিফও ছিল।
সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ফারুকী দাবি করেছেন, এবার শোভাযাত্রাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি।
তিনি বলেন, “ফ্যাসিস্ট কোনো রাজনীতির অংশ নয়, ফ্যাসিস্ট সবচেয়ে বড় অশুভশক্তি। তাই আমরা শুধু ফ্যাসিস্টের মুখাবয়ব ব্যবহার করেছি।”
প্রবীণ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার এক কলামে মঙ্গল শোভাযাত্রার পেছনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে লিখেছেন, “১৯৮৯ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রথম বর্ষবরণের শোভাযাত্রা আয়োজন করে, তখন এটি ছিল এক শিল্পতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ। সামরিক শাসনের অন্ধকার সময়ের পর, সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার জয়গান ও অশুভের বিরুদ্ধে অবস্থান— এই ছিল মূল বার্তা। ওই শোভাযাত্রায় ‘গণতন্ত্র চাই’, ‘জয় হোক মানবতার’— এমন স্লোগানও ছিল। অর্থাৎ, মঙ্গল শোভাযাত্রা একটি প্রতীকী রাজনৈতিক উচ্চারণ।”
“আজকের তরুণ প্রজন্ম অনেক বেশি তথ্যপ্রবাহের মাঝে রয়েছে, কিন্তু আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। তারা জানে না তাদের ভাষা, গান, লোকশিল্প, উৎসব কীভাবে একদিন রাজনীতি ও সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার ছিল,” লিখেছেন তিনি।
রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, সংস্কৃতি কখনোই রাজনীতি থেকে আলাদা নয় এবং সে কারণে রাজনীতিকে আলাদা করাও যাচ্ছে না।
“এগুলো নিয়ে হৈ হুল্লোড় করছে কিছু রাজনৈতিক দল। চারুকলার আয়োজন তাদের। দলগুলো বা সরকার তাতে না জড়ালে কোনো সমস্যা হতো না। যারা পছন্দ করবে না তারা সেখানেই না গিয়ে নিজেদের মতো উদযাপন করতে পারে।”
তবে বর্ষবরণের এই আয়োজনে রাজনৈতিক প্রভাব বিভেদ তৈরি করেছে বলেই মনে করেন অনেকে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক এ কে এম শাহনেওয়াজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, রাজনৈতিক ব্যবহার ও বিভাজন যে প্রকট, সেটা এবারের আয়োজন নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।
“এখন যা হচ্ছে তা ইতিহাস বিচ্ছিন্নতার ফল। নববর্ষ, বর্ষবরণ ও শোভাযাত্রা সম্পর্কে না জানার প্রতিফল। এর পেছনে প্রতিবাদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে উপাদান তার চর্চা নেই বলেই যখন যে শক্তি আসে তারা এগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে চায়। সেটিই হচ্ছে এখন।”
রাজনীতির কারণেই পহেলা বৈশাখের উৎসবের মধ্যেও যে বিভেদের রেখা তৈরি হয়েছে, তা সামাল দিতে না পারলে সামনে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠার আশঙ্কাও আছে কারও কারও মধ্যে।
তবে অধ্যাপক শাহনেওয়াজ বলেন, সাংস্কৃতিক আয়োজনগুলো নিয়ে এখন যা হচ্ছে তাতে এগুলো আরও রাজনৈতিক রূপ পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এগুলো সুন্দর রূপে ফিরে আসবে।
“যা হচ্ছে এভাবে তা চলতে পারে না। তবে এগুলোতে আসলে পাল্টা প্রতিক্রিয়া যে হয় সেটা রমনা বটমূলে বোমা হামলার পরের বছরগুলোতে দেখেছি। মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সম্পৃক্ত হয়েছে। তাই এখন কিছুকাল সংকট হলেও ঠিকই আপন মহিমায় এগুলো যথাযথভাবে ফিরে আসবে।”