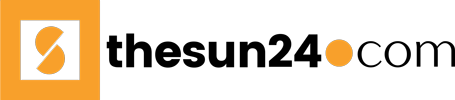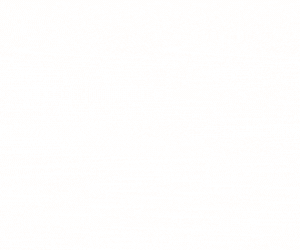বাংলাদেশের বিচার বিভাগের উপর দিয়ে সাম্প্রতিককালে যে ঝড় বয়ে গেছে তা অতীতের যেকোনো সময়ের সব ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। বিচারাঙ্গনে সংশ্লিষ্ট সবার শির অবনত হয়েছে গ্লানিময় বিভীষিকার পাশবিক মঞ্চায়নে। দেশের মানুষের শেষ ভরসাস্থল যেন অপরিচিত এক অঙ্গনে পরিণত হয়ে ব্যঙ্গ করছে দাঁত বের করে। পৃথিবীর বুকে জাতি হিসেবে আমরা সভ্য হতে হতে সামনের দিকে যাব – এটাই কি হওয়ার ছিল স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি? ৫৩ বছর পর কী দেখলাম? বিচারপতির ঘাড়ে রাজপথের আন্দোলনকারীর পাঞ্জা। বিচারাঙ্গনের এই পরিণতি আমাদের কী ইঙ্গিত দেয়? আমাদের এ দেশ কোথায় যাচ্ছে?
বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আজ নতুন কোনো বিষয় নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই ব্যবস্থাকে করায়ত্ব রেখে নির্বাহীরা এবং রাজনীতিবিদরা সব সুয়োগকে হাতের মুঠোয় রাখার সম্ভব সব কলকব্জা ব্যবহার করে আসছেন।
রাষ্ট্রের তিন মূল স্তম্ভের একটি হলো বিচার বিভাগ; অপর দুটি নির্বাহী ও আইন বিভাগ। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নির্বাহী বিভাগ শক্তিশালী হয়। দেশে চালানোর জন্য এটি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আইন ও বিচার বিভাগকে ঠিকমতো কাজ করতে দেওয়াও তেমিই গুরুত্বপূর্ণ। আইন বিভাগের উপর প্রশানের আধিপত্য নিয়ে আজকের লেখা নয়। বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকার ইচ্ছা এ আলোচনায়।
দেশের মানুষের সাংবিধানিক ও সর্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিতে বিচার বিভাগকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে; তা না হলে সুবিধাবাদী নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদরা এই বিচার বিভাগকে হাতিয়ার করে নিরীহ জনগণকে যাঁতাকলে পিষ্ট করবে। এটা ইতিহাসের শিক্ষা, মানবজাতির ক্রমবিকাশে যার প্রমাণ মেলে। তাই পৃথিবীর তাবৎ উন্নত দেশে বিচার বিভাগের উপর নির্বাহীর কিংবা রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। আমাদের দেশে নির্বাহী এবং রানীতিবিদদের নগ্নভাবে বিচারাঙ্গনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে দেখি আমরা।
বিচারক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মাথায় রাখেন এ বিষয়টিতে তার চাকরি সংশ্লিষ্ট কোনো নির্বাহী কিংবা রাজনীতিক জড়িত আছেন কি না; কিংবা বিচারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কেউ কোনো চাপ দিয়েছেন কি না। এই অবস্থা উচ্চ আদালত থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পর্যন্ত ব্যাপৃত। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য প্রভাবশালীরা যেকোনো অস্ত্র ব্যবহার করতে ছাড়েন না। এই অস্ত্রের অন্যতম হলো বিচার ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি করায়ত্ব করতে পারে নির্বাহী কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদরা। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ কারণে রাজনীতি ও নির্বাহী কর্মকর্তারা ব্যাপক প্রতাপশালী হয়ে থাকেন। এ কারণে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সবসময় বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার কথা বলে আসছেন।
বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে ১৯৯৪ সালে একটি রিট মামলা করেছিলেন তৎকালীন জেলা জজ এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মাসদার হোসেন। ১৯৯৯ সালে নির্বাহী এ মামলার রায় হয়। সেই রায় বাস্তবায়নে ১২ দফা নির্দেশনা দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়। ওই ১২ নির্দেশনায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই।
এক. সংবিধানের ১৫২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় সব বিভাগের কাজ সার্ভিস অব রিপাবলিকের ভেতরে পড়বে। তবে বিচার বিভাগের কাজ ও অবকাঠামোর সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের সিভিল সার্ভিসের অনেক ভিন্নতা রয়েছে। বিচার বিভাগকে অন্যান্য সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে এক করা যাবে না।
দুই. বিচারিক (জুডিশিয়াল) ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে এবং নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারিক কাজ করতে পারবেন না। সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ পদ্ধতি, নিয়োগ বদলিসহ অন্যান্য কাজের বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবেন।
তিন. সিভিল সার্ভিস অর্ডার ১৯৮০ অনুযায়ী সব ম্যাজিস্ট্রেটকে পিএসসির অধীনে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে একসঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হয়। একসঙ্গে নিয়োগ দেওয়া সংবিধান পরিপন্থী।
চার. এই রায় পাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা এবং কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশনে সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। এই কমিশনে নারী ও পুরুষ বলে কোনো বৈষম্য থাকবে না।
পাঁচ. সংবিধানের ১১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়ারির সবার চাকরির বিধিমালা (নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটিসহ অন্যান্য) প্রণয়ন করবেন।
ছয়. সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন করবেন।
সাত. সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের থাকবে।
আট. বিচার বিভাগ জাতীয় সংসদ বা নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকবে না এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটসহ সব বিচারক স্বাধীনভাবে কাজ করবেন।
নয়. জুডিশিয়ারির (নিম্ন আদালত) বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ওপর নির্বাহী বিভাগের কোনো হাত থাকবে না। এই বাজেট সুপ্রিম কোর্ট প্রণয়ন ও বরাদ্দ করবে।
দশ. জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যরা প্রশাসনিক আদালতের আওতাভুক্ত থাকবেন।
এগারো. মাসদার হোসেন বনাম রাষ্ট্র মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগ পৃথককরণের জন্য সংবিধানে কোনো সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। তবে পৃথককরণ আরও অর্থবহ করতে যদি সংবিধানের সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তবে তা করা যাবে।
বারো. জুডিশিয়াল পে-কমিশন: জুডিশিয়াল পে-কমিশন জুডিশিয়ারির সদস্যদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ না করবে, ততদিন পর্যন্ত বর্তমান অবকাঠামো অনুযায়ী তার সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।
নথিগতভাবে বিচার বিভাগ নির্বাহী কিংবা আইন বিভাগ থেকে পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে আইন মন্ত্রণালয় ও সরকারের ইচ্ছ-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। সুপ্রিম কোর্টোর রায়ের ১২ দফা নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি।
১২ নির্দেশনার অষ্টম দফায় রয়েছে সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন বিচার বিভাগ হবে। অথচ এখনও নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জজদের বদলি, বেতন, ছুটি, পদোন্নতি হয়ে থাকে। তাই মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও কার্যকর হয়নি; এবং এই ৮ নম্বর দফাটিই বিচার বিভাগকে হাতের মুঠোয় রাখার মোক্ষম অস্ত্র। এ থেকে আমাদের নির্বহী ও রাজনীতিবিদদের মানসিকতা পরিষ্কার বোঝা যায়। আমাদের আদালতের দিকে তাকালে এটি আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এরশাদ সরকারের পতন, খালেদা সরকারের পতন, সবশেষে হাসিনার পতনের পরবর্তী সময়ের বিচারিক আদালত ও উচ্চ আদালতের ঘটনাসমূহ একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে।
দুর্নীতির মামলায় এরশাদ বছরের পর বছর কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। একটির পর একটি মামলা দিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা হতো। তখন ছিল বিএনপি সরকার। ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি কয়েকটি মামলায় কারাগারে ছিলেন। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তিনি ছাড়া পান। এই ঘটনায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় পরিষ্কার। বিএনপি রাজনৈতিকভাবে চায়নি বলে এরশাদ কারাগারে ছিলেন; পক্ষান্তরে রানৈতিক সুবিধার দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় ১৯৯৬ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি মুক্ত হন। এটি বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগ এবং রাজনীতির প্রভাবের নগ্ন উদাহরণ।
বলতে পারি ওই সময় তো মাসদার হোসেন মামলার ঘটনা ঘটেনি; বিচার বিভাগও পৃথক হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের সময়ে দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়াকে বিচারিক আদালত ৫ বছরের সাজা দিলেও হাই কোর্ট তা বাড়িয়ে ১০ বছর করে। একই ধরনের আরেকটি দুর্নীতির মামলায় তাকে ৭ বছরের সাজা দেয় বিচারিক আদালত।
এর একটি হলো জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলা। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় পাঁচ বছরের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে। ওই বছরের অক্টোবরে হাই কোর্টে আপিল শুনানি শেষে সাজা বেড়ে হয় ১০ বছর। একইভাবে অপর মামলাটি ছিল জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা। এই মামলায় তার সাজা হয় ৭ বছর। এ দুই মামলায় হাই কার্টে আপিল করলেও তিনি জামিন পাননি। এটিও বিচার বিভাগকে কুক্ষিগত করার নগ্ন উদাহরণ।
এসব বাধা দূর করতে বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনসহ একটি পথরেখা (রোডম্যাপ) দিয়েছেন গত সেপ্টেম্বরে নিম্ন আদালতের বিচারকদের উদ্দেশে দেওয়া তার অভিভাষণে।
তার পথরেখায় দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবে আশার আলো দেখতে পারে। তবে যতদিন তা বাস্তবে রূপলাভ না করবে ততদিন আশায় থাকতে মন্দ কী!
- দেবাশীষ দেব সাংবাদিক, আইনজীবী। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে কর্মরত ২০০৬ সাল থেকে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে সিনিয়র লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স করসপন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত। পাশাপাশি আইন পেশায় যুক্ত।