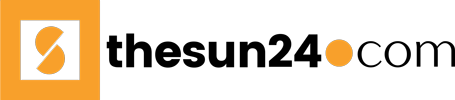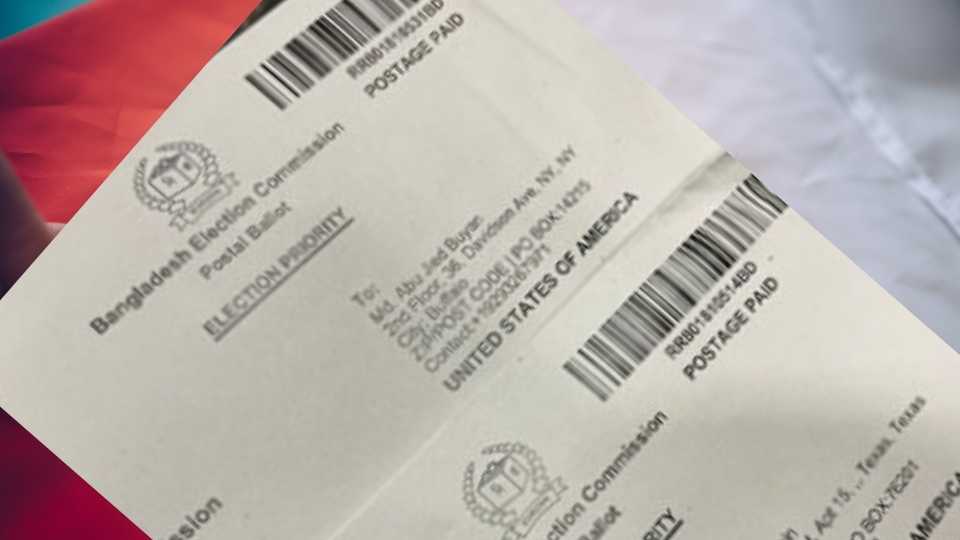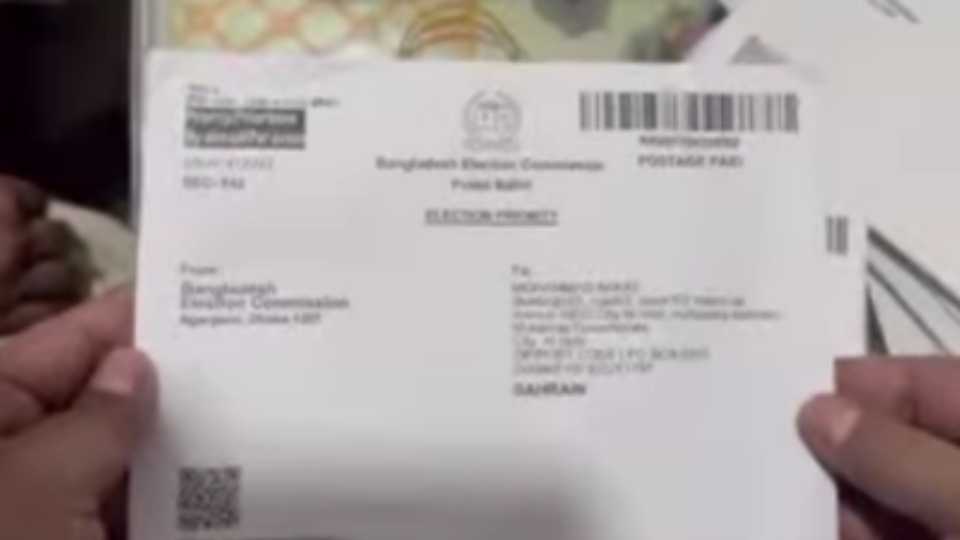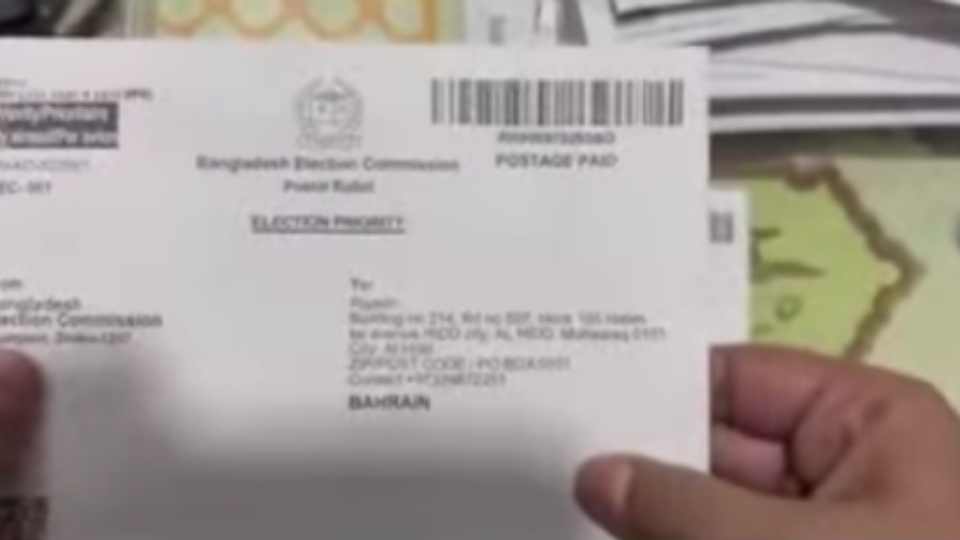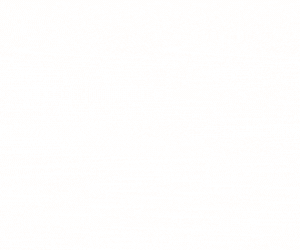মিয়ানমারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণ কী তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ, হাজির করা হচ্ছে নানা তত্ত্ব-উপাত্ত। তেমনি কী কারণে থাইল্যান্ডের ব্যস্ত নগরী ব্যাংককে বহুতল ভবন বিধ্বস্ত হলো তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ এবং কৌতুহল দুটোই রয়েছে জনমনে।
শুক্রবার মিয়ানমারে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে অসংখ্য অবকাঠামো।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমারের অবস্থান ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে। তাদের প্রতিবেশি থাইল্যান্ড ও চীনের অবস্থানও ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে হয়ে থাকলেও তারা এতোটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে নেই।
ব্যাংকক শুক্রবারের ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে এক হাজার কিলোমিটার বা ৬২১ মাইল দূরে অবস্থিত। তারপরও ভূমিকম্পে সেখানকার নির্মাণাধীন বহুতল ভবন ধসে পড়েছে।
আমরা এখানে সেটাই দেখার চেষ্টা করব। কী কারণে এই ভূমিকম্প এবং এর প্রভাব এতো দূরের একটা শহরের কীভাবে পড়তে পারে।
ভূমিকম্পের কারণ কী?
পৃথিবীর ওপরের অংশটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যেগুলোকে টেকটোনিক প্লেট বলা হয়। এ প্লেটগুলো প্রতিনিয়ত নড়ছে। কিছু প্লেট পাশাপাশি ঘুরে কিছু উপর-নিচ। আর এ নড়চড়ের কারণেই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো ঘটনা ঘটে।
ইউরেশীয়, ভারতীয়, সুন্দা প্লেট এবং বার্মা মাইক্রোপ্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মিয়ানমারকে ভূতাত্ত্বিকভাবে অন্যতম ‘সক্রিয়’ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ভূতত্ত্ব অনুসারে ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটের সংঘর্ষ থেকে জন্ম হিমালয় পর্বতমালার। আর ২০০৪ সালে ভারতীয় প্লেট বার্মা মাইক্রোপ্লেটের নিচে সরে যাওয়ায় হয় সেই ভয়াবহ সুনামি।
লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের টেকটোনিকস রিডার ড. রেবেকা বেল বলেন, এই নড়াচড়ার জন্য ফাটল বা বিচ্যুতি হয়ে থাকে, যার জন্য টেকটোনিক প্লেটগুলো পাশে ‘সরতে’ পারে।
মিয়ানমারের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ১২শ’ কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘের এমন একটি বিচ্যুতি রয়েছে, প্রধান এই বিচ্যুতি ‘স্যাগেইং ফল্ট’ নামে পরিচিত।
প্রাথমিকভাবে যেটি দেখা গেছে শুক্রবারের ৭.৭ মাত্রার যে ভূমিকম্পটি যে জায়গা বদলের জন্য হয়েছিল সেটা হচ্ছে ‘স্ট্রাইক-স্লিপ’, যা আনুভূমিকভাবে দুইটি ব্লকের পাশাপাশি সরে যাওয়ার কারণে ঘটে। যা ‘স্যাগেইং ফল্ট’ এর স্বাভাবিক নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
এই প্লেটগুলো জায়টা বদলের সময় আটকে যেতে পারে। যতক্ষণ আটকে থাকে ঘর্ষণ হয়, হঠাৎ যখন মুক্ত হয় পৃথিবী নড়ে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পটি এতো দূরে কেন অনুভূত হলো?
ভূমিকম্প ভূতলের ৭০০ কিলোমিটার গভীরে পর্যন্ত হতে পারে। শুক্রবারের ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল ভূমি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। যার কারণে ভূপৃষ্ঠে কম্পনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে ভূতাত্ত্বিক জরিপের তথ্যানুসারে, মিয়ানমারের ভূমিকম্পটির মাত্রা মোমেন্ট স্কেলে ৭.৭ ছিল, খুবই শক্তিশালী। যা হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি শক্তি উৎপন্ন করেছিল।
রেবেকা বেল বলেন, মিয়ানমারের ওই বিচ্যুতির কারণেই ভূমিকম্পটি এতো শক্তিশালী ছিল।
তিনি বলেন, “বিচ্যুতিটির সোজা আকৃতির জন্য ভূমিকম্পটি বড় এলাকা নিয়ে অনুভূত হয়। বিচ্যুতিটি যত বড় এলাকায় সরে ভূমিকম্পও তত বিশাল এলাকা নিয়ে অনভূত হয়ে থাকে।”
গত শতাব্দীতে এই অঞ্চলে সাত বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার অন্তত ছয়টি ভূমিকম্প হয়েছে বলেও রেবেকা বেল জানান।
আর সরল রেখা আকৃতির বিচ্যুতি মানে শক্তি পরিবহনের সক্ষমতাও বেশি, যা ১২শ কিলোমিটার দক্ষিণে থাইল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।
তাছাড়া ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠে কেমন অনুভূত হবে তা সেখানকার মাটির উপর ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।
নরম মাটিতে কম্পন ধীরে প্রবাহিত হয় এবং সঞ্চিত হয়ে বড় আকারে রূপ নেয়। ব্যাংককের ভূতাত্ত্বিক অবস্থাই সেই কম্পণকে আরও বর্ধিত করে তুলেছে।
ব্যাংককে একটি বহুতল ভবনই কেন ধসে পড়ল?
ভূমিকম্পের সময় ব্যাংককের একটি বহুলত ভবনের সুইমিংপুলের পানি উপচে পড়ছে এবং চাতুহক এলাকায় নির্মাণাধীণ একটি সরকারি বহুতল ভবন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ার ভিডিও দেখা যাচ্ছে। একটি ভবনই কেন বিধ্বস্ত হলো এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে।
লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের ভূমিকম্প প্রকৌশল বিভাজের সিনিয়র লেকচারার ড. ক্রিশ্চিয়ান মালাগা-চুকুইতায়পে বলেন, ২০০৯ সালের আগে থাইল্যান্ডে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ভবন নির্মাণের সমন্বিত নিরাপত্তা মান মানা হতো না।
তাই ওই ধরনের পুরনো ভবনগুলোই ঝুঁকিপূর্ণ বলেও জানান তিনি।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এমিলি সো বলেন, পুরনো ভবনগুলোও শক্তিশালী করা সম্ভব। নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়াতেও এমনটি করা হয়েছে।
থাইল্যান্ডের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপর আমর্ন পিমার্নমাস জানান, যে ভবনটি ধসে পড়েছে সেটি নতুন এবং নির্মাণাধীন। তবে তিনি মনে করেন ব্যাংককের নরম মাটি ভবনটি ধসে পড়ায় ভূমিকা রাখতে পারে।
এর পেছনে ভবন নির্মাণ সামগ্রির এবং নির্মাণের অনিয়মসহ আরও কারণ থাকলেও তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান তিনি।
এদিকে ধসে পড়ার ভিডিও বিশ্লেষণ করে ড. মালাগা বলেন, ভবনটি মনে হচ্ছে ‘ফ্ল্যাট স্লাব’ প্রক্রিয়া বানানো হচ্ছিল, যা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার জন্য সুপারিশ করা হয় না।
তিনি বলেন, ফ্ল্যাট স্লাব হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো বীম না বানিয়ে সরাসরি কলামের ওপর ফ্লোর তৈরি করা হয়। ধরুন চারপাশের কাঠামো না দিয়ে শুধু চারটি পায়ের ওপর টেবিল বানানোর মতো।
এ ধরনের ভবন তৈরির খরচ এবং প্রকৌশলগত সুবিধা দিলেও ভূমিকম্পের সময় টিকে থাকা মুশকিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
বিবিসি অবলম্বনে