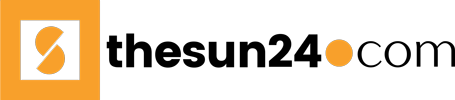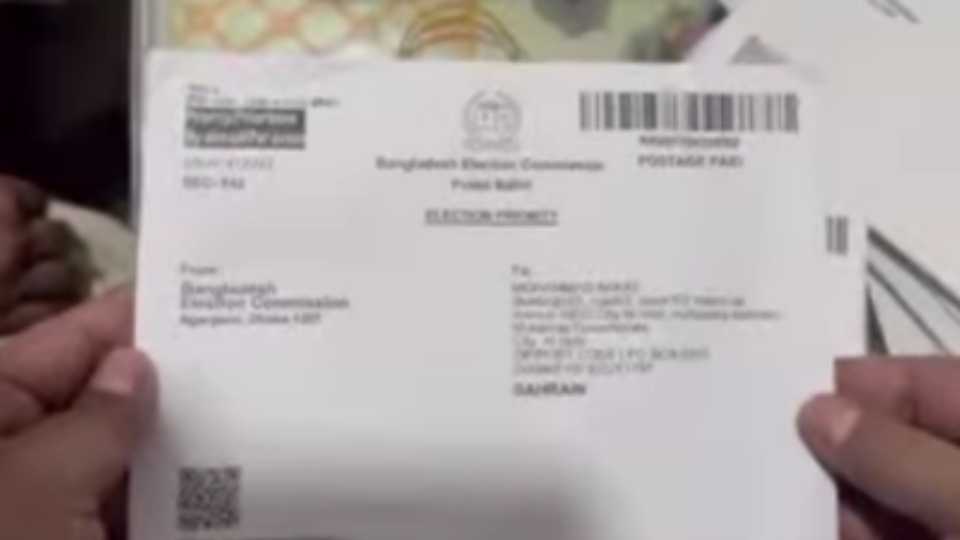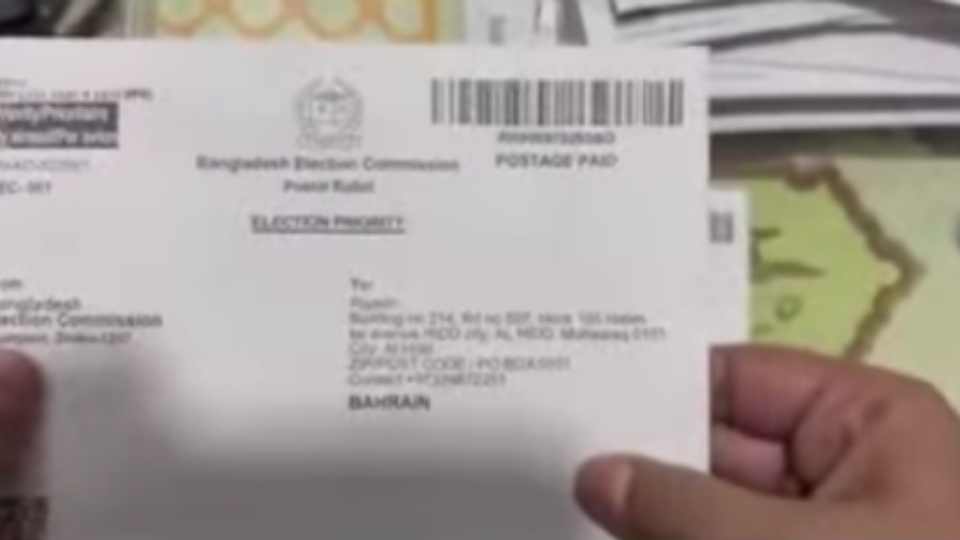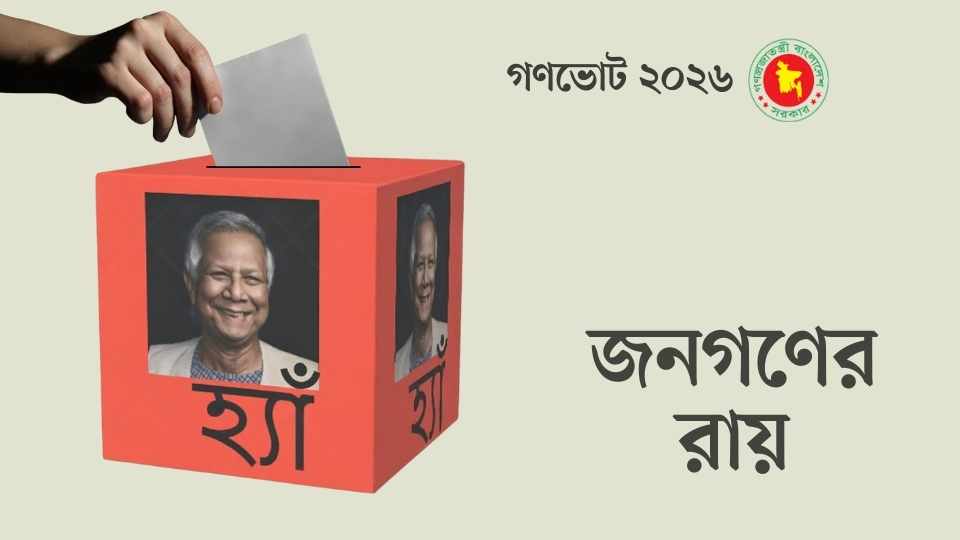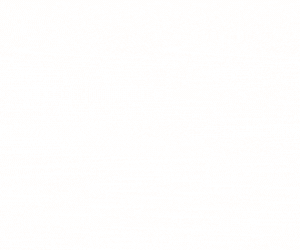মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৭; ধ্বংস ক্ষমতার নিরিখে একে শক্তিশালী ভূমিকম্পই বলা হয়ে। এই ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড মান্দালয় শহর; মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদো’র উত্তরের ১০০ বর্গ কিলোমিটারের এই শহরে বাস করে ১৫ লাখের মতো মানুষ।
শুক্রবারের এই ভূমিকম্পে ঠিক কতজন মারা গেছে, তার সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
ইরাবতীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পে মিয়ানমারের দ্বিতীয় জনবহুল শহর মান্দালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, হোটেলসহ বহু ভবন ধসে পড়েছে।
ইরাবতী নদীর ওপর প্রায় শতবর্ষী আভা সেতুও নেই হয়ে গেছে ভূমিকম্পে। ১৬টি স্প্যানের ওপর দাঁড়ানো ৮৯০ মিটার দীর্ঘ এই সেতু ব্রিটিশরা নির্মাণ করেছিল ১৯৩৪ সালে।
এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল সাগাইং শহরের কাছে, ভূপৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার গভীরে। মিয়ানমারের বড় শহরগুলোর মধ্যে মান্দালয়ে আঘাত সবচেয়ে তীব্র হলেও রাজধানী নেপিদোর ক্ষতিও কম হয়নি। সেখানে নিহতের সংখ্যা ১০০ ছুঁই ছুঁই করছে। মিয়ানমার ছাড়িয়ে থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনও কাঁপিয়েছে এই ভূমিকম্প।
৭ দশমিক ৭ মাত্রার চেয়ে বেশি শক্তির ভূমিকম্পও বিশ্ব দেখেছে। রিখটার স্কেলে মাত্রা ৮ ছাড়িয়ে গেলে তাকে মহা ভূমিকম্প বলে। আবার ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায়, তাতে বিশাল সুনামি হয়েছিল, সব মিলিয়ে মারা গিয়েছিল ২ লাখের বেশি মানুষ। তার চেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পও হয়েছিল ১৯৬০ সালে চিলিতে।
মান্দালয়ের সঙ্গে যদি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এই নগরী আয়তনে তার ৩ গুণ, আর জন সংখ্যা ১০ গুণ।
যদি ঢাকায় এমন একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, তবে অবস্থা কী দাঁড়াবে? গবেষকরা বলছেন, ভয়াবহ।
ইতিহাস বলছে, এমন মাত্রার ভূমিকম্প আগে ঘটেছে এই দেশে। ফলে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ইতিহাস
গবেষকরা দেখছেন, বাংলাদেশ লাগোয়া অঞ্চলে বড় ভূমিকম্পের মধ্যে রয়েছে ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের ভূমিকম্প। তার মাত্রা ছিল ৮ এর বেশি। ১৭৮৭ সালে ৭.৫ মাত্রার আসাম ভূমিকম্প। তার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদীরে গতিপথই পাল্টে গিয়ে আজকের যমুনা নদী হয়।
১৯২৩ সালে ঢাকা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দুরে কিশোরগঞ্জের কাছে ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর ফলে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ কেঁপে ওঠে এবং ঢাকায় বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।
সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলগুলো ছোট থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প মাঝে মধ্যেই হয়েছে। ২০১০ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত চাঁদপুরের মোহনা অঞ্চলে চার থেকে পাঁচটি ৪.২ থেকে ৫.১ মাত্রার মাঝারি ভূমিকম্প হয়েছে। এরমধ্যে ২০১০ সালের ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকাসহ আশপাশের অঞ্চলে অনুভূত হয়।
বাংলাদেশ কতটা ঝূঁকিতে?
যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিস ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর আর্থকোয়েক রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিইআরআই)’য়ে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট সাব্বির আহমেদ কিছুকাল আগে বাংলাদেশের ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিয়ে লিখেছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক এই শিক্ষার্থীর মতে, অবস্থা বেশ ঝুঁকিপূর্ণই।
কোনো অঞ্চল ভূমিকম্পের কতটা ঝুঁকিতে রয়েছে, তা নির্ভর করে তার ভূতাত্ত্বিক গঠন। বাংলাদেশের অবস্থান তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল। ভূঅভ্যন্তরের টেকটোনিক প্লেটগুলোর ওপরই গোটা ভূপৃষশ্ঠ ভাসছে।
সাব্বির আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে ইউরেশিয়ান (ইউরোপ এবং এশিয়া) প্লেট। পূর্ব দিকে রয়েছে মিয়ানমার বা বার্মা প্লেট এবং আর ভারতীয় প্লেটের ওপর তো বাংলাদেশ বসে আছে।
আবার বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত বরাবর রয়েছে বিশাল এক ডাউকি চ্যুতি, যা শিলং মালভূমির কারণে গঠিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিলং এবং আশপাশে প্রতিনিয়ত ছোট মাত্রার ভূমিকম্প হচ্ছে।
সাব্বির আহমেদ বলেন, এই ছোট ছোট ভূমিকম্প আমাদের জানান দিচ্ছে, শিলং ও আশপাশের এলাকাতে অধিক পরিমাণে চাপ সঞ্চিত হচ্ছে, যা কি না যেকোনো সময় বড় মাত্রার ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।
বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল নিয়ে তিনি বলেন, “পূর্বদিকে উত্তরে সিলেট থেকে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রয়েছে বিস্তৃত পাহাড়পুঞ্জ। অনেকেরই জানা নেই যে এই পাহাড়পুঞ্জ মূলত ভারত ও মিয়ানমার প্লেটের সংঘর্ষের ফলে গঠিত হয়েছে। অনেক ছোট ছোট এমনকি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প প্রায়ই হয় এই অঞ্চলে। ধারণা করা হয়, এক বিশাল চ্যুতি চট্টগ্রাম পাহাড়ের সমান্তরালে গিয়ে দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে সুন্দা চ্যুতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।”
“বাংলাদেশ থেকে একটু উত্তরে গেলে তো কথাই নেই, বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, যা কি না তৈরি হয়েছে ভারত ও ইউরোপ প্লেটের সংঘর্ষে। বাংলাদেশ যেহেতু পলি দ্বারা গঠিত, তা ভূকম্পনকে ত্বরান্বিত করে, ফলে ক্ষতির সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।। ভূতাত্ত্বিক অবস্থানের এবং গঠনের বিচারে বাংলাদেশ এমন একটি অবস্থানে রয়েছে, যা কিনা ভূমিকম্পের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ,” বলেন তিনি।
বাংলাদেশের উত্তরে শিলং মালভূমির পাদদেশের অঞ্চলগুলো এবং পূর্বদিকে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অঞ্চলগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ, যা গবেষকরা বলছেন।
ঢাকার অবস্থান নিয়ে সাব্বির আহমেদ বলেন, “এখানে ঝুঁকি একেবারে কম না। বিশেষ করে এর আশেপাশে গত কয়েক বছর ছোট থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অন্তত তাই বলে। শুধু তাই নয়, ঢাকার আশপাশে রয়েছে বড় ধরনের বেশ কয়েকটি চ্যুতি, যা কি না ঢাকাকে যেকোনো সময় বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে।”
ঢাকার উত্তরে বিস্তৃত টাঙ্গাইল অঞ্চলে রয়েছে মধুপুর চ্যুতি। এই মধুপুর চ্যুতিতে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকার জন্য দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আনতে পারে বলে সাব্বির আহমেদের অভিমত।
“ঢাকার মাটি থেকে যে হারে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে, তাতে পানির স্তর দিনে দিনে নিচে নেমে যাচ্ছে, যা ঢাকার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকি ছোট মাত্রার ভূমিকম্পেও অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে,” যোগ করেন তিনি।
ঢাকায় হলে কতটা ভয়াবহ হবে?
মিয়ানমারের শুক্রবারের ভূমিকম্পে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরের ঢাকাও খানিকা কেঁপে উঠেছিল।
বড় ভূমিকম্প হলে ঢাকার অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেই ভয়াবহতা ফুটে ওঠে জধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) এক গবেষণামূলক প্রকল্পে। গত বছর ওই প্রকল্পের এক সেমিনারে গবেষণা ও জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেছিলেন গবেষকেরা।

তাতে বলা হয়, মিয়ানমারে চেয়ে কম মাত্রার ভূমিকম্পেও ঢাকার মোট ভবনের ৪০ শতাংশ ধসে পড়বে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্পকে বলা হয় সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। কেননা, এর আগাম কোনো সতর্কতা পাওয়া যায় না। আর এই দুর্যোগে হাসপাতাল কিংবা ফায়ার স্টেশন ধসে পড়লে উদ্ধার অভিযান চালানো কিংবা আহতদের চিকিৎসা দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।
গবেষকরা বলছেন, মধুপুরের চ্যুতিতে যদি রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পও হয়, তাহলে ঢাকায় কমপক্ষে ৮ লাখের বেশি ভবন নেই হয়ে যাবে। ওই মাত্রার ভূমিকম্প দিনে হলে কমপক্ষে ২ লাখ ১০ হাজার মানুষের মৃত্যু হবে। আর রাতে হলে মৃতের সংখ্যা আরও ১ লাখ বাড়বে।
জনবহুল ঢাকা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠায় ঢাকায় ভূমিকম্পের ভয়াবহত অনুমানের চেয়ে বেশি হবে বলে গবেষকরা সতর্ক করছেন। কারণ এখানে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা এতই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে যে বড় মাত্রার ভূমিকম্পে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে।
২০২৩ সালে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে তুরস্কে অর্ধ লক্ষাধিক ও সিরিয়ায় প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।
সেই ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “তুরস্ক-সিরিয়ার মতো ভূমিকম্প যদি এখানে ঘটে, কয়েক গুণ মানুষ মারা যেতে পারে। কারণ হচ্ছে, আমাদের ভূমিকম্প সহনীয় ভবন হাতে গোনা। অথচ এখানে হাজার হাজার বহুতল ভবন আছে।”
তুরস্কে অনেক ভবন ধসে পড়লেও পাশেই অনেক ভবন দাঁড়িয়ে ছিল। তার মানে, ওই ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। দুর্নীর দেশ বাংলাদেশে এমন ভবন হাতেগোনা হবে ধারণা থেকে বিশেষজ্ঞরা শঙ্কিত।
অধ্যাপক মুজিবুরের ভাষ্যে, “এখন যে অপরিকল্পিতভাবে নগরগুলো গড়ে উঠছে, সেখানে বড় কোনো ভূমিকম্প ঘটে গেলে, উদ্ধার কার্যক্রম চালানোও তো খুব কঠিন হয়ে যাবে। অনেক সুযোগ-সুবিধাও তো আমাদের নেই। ফলে ভবনের কাঠামোগত সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
“আমরা তো শিল্পোন্নত দেশের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের শিল্পকারখানাগুলো কী করে? শুধু টাকা বাঁচানোর জন্য বা মুনাফা বেশি করার জন্য ইটিপি চালু রাখা হয় না। এতে মানুষ ও পরিবেশের বিপর্যয় আমরা ডেকে আনছি।”
বাংলাদেশ ভূমিকম্প সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী গত বছর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভূমিকম্পের ক্ষতি কমাতে বিল্ডিং কোড মানাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে ৯৯ শতাংশ নতুন ভবন টিকে যায়। আর পুরনো ভবন মজবুতিকরণের দিকে যেতে হবে।