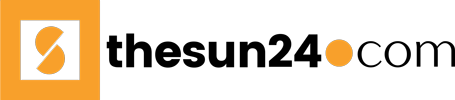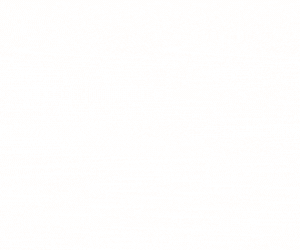অনেকের ধারণা, ফ্যাসিবাদ কেবল ইতিহাসের এক অধ্যায়, যা আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়। বাস্তবতা হলো আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নেতা-নেত্রীর উত্থানে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য এখনও দেখা যায়। কিন্তু কি এই ফ্যাসিবাদ।
যদি এককথায় বলি তবে বলতে হবে ফ্যাসিবাদ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ, যা চরম জাতীয়তাবাদ, কর্তৃত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দমন- এরকম ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ সবচেয়ে ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিশেষ করে ইতালি ও জার্মানিতে। এই মতাদর্শ কেবল রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং সমাজব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলাফল মানুষের মনে এখনও কাঁপুনি তোলে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জনগণের হতাশা এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল যা শাসক শ্রেণিকে চরমপন্থী সমাধানের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।
ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, ১৯২২ সালে ইতালির বেনিতো মুসোলিনি প্রথম ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ‘ফ্যাসিও দে কমবাতিমেন্তো’ (Fascio di Combattimento) নামের সংগঠনটি ফ্যাসিবাদ শব্দের উৎপত্তির উৎস। ‘ফ্যাসিও’ শব্দটি এসেছে লাতিন ‘ফ্যাসেস’ থেকে, যা বাংলায় তরজমা করলে দাঁড়ায় একত্রিত শক্তি বা ঐক্য।
এরপর আরও একটু এগোলে ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার এবং তার নাৎসি দলের (Nazi Party) ক্ষমতায় অধিষ্টিত হওয়ার ইতিহাস সামনে আসে। অনেকেই হয়তো জানেন না হিটলারের উত্থান ছিল নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। যদিও ক্ষমতায় বসে তিনি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
মূলত ফ্যাসিবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রবল জাতীয়তাবাদ। ফ্যাসিবাদী নেতারা জাতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং জাতির স্বার্থের বাইরে কোনো মতাদর্শ বা নীতি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করেন।
ইদানিং যে ফ্যাসিবাদের কথা বলা হয় তাতে ফ্যাসিস্টের চরম কর্তৃত্ববাদ চরিত্রটি নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। তার মানে আইনের শাসনের পরিবর্তে নেতার আদেশই নিয়মে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকে কেউ কেউ ফ্যাসিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। অথচ জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের মতো বিষয়ই মূলত ফ্যাসিবাদের মূল দিক, যেখানে জাতিগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যকে উসকে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।
এ ছাড়া গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা হরণের মতো পদক্ষেপও ফ্যাসিবাদের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। বিরোধী মত দমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদাহরণই ফ্যাসিবাদের চরিত্র বহন করে।
এর বাইরে রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক শক্তির প্রয়োগ, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আরোপের মতো বিষয়াদি ফ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। সহজ ভাষায় বললে ফ্যাসিবাদ একদিকে সাম্যবাদ (কমিউনিজম) ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী, আবার অন্যদিকে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক মূল্যবোধেরও পরিপন্থী।
এবার একটু ঘুরে দেখাতে চাই ইতিহাসে ফ্যাসিবাদের প্রয়োগ কেমন ছিল। শুরুটাই বা কোথা থেকে। ইতালির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুসোলিনি ১৯২২ সালে ‘মার্চ অন রোম’-এর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন এবং ধীরে ধীরে সব বিরোধী দল ও গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। তার সরকার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, গোপন পুলিশ ও রাজনৈতিক সহিংসতার মাধ্যমে জনগণের মুখ রীতিমতো বন্ধ করে দেয়। মুসোলিনির সেই ফ্যাসিবাদ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের এক স্বপ্ন, যেখানে ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।
অন্যদিকে জার্মানিতে হিটলার এবং তার নাৎসি পার্টি জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা করে, এবং ইহুদিদের জাতির শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করে। হিটলারের উত্থানের পিছনে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ভার্সাই চুক্তি নিয়ে অসন্তোষ, এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ভূমিকা রেখেছিল।
বলা হয়ে থাকে হিটলারের শাসনে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ দেগেছে গোটা বিশ্ব, যেখানে কোটি কোটি মানুষ নাৎসি ঘৃণানীতির শিকার হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হোলোকাস্ট ও গণহত্যা- এসবই ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরিণতির উদাহরণ।
ইউরোপের বাইরে, এশিয়াও ফ্যাসিবাদের ছায়া থেকে মুক্ত ছিল না কখনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে কিছু দেশে ফ্যাসিবাদী শাসনের বা আচরণের চিহ্ন পাওয়া যায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান সামরিক নেতৃত্বাধীন একটি চরম জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। সরকার ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং বিদেশি জাতিগোষ্ঠীর প্রতি অবজ্ঞা- এসবই জাপানের ফ্যাসিবাদের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। উদাহরণ দিয়ে বললে মোটা দাগে সামনে আসে মানচুরিয়া দখল (১৯৩১), নানজিং গণহত্যা (১৯৩৭) এবং প্যাসিফিক যুদ্ধের মতো ঘটনাবলী। তা ছাড়া রাজনৈতিক বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন এবং ব্যাপক মাত্রায় ‘সেন্সরশিপ’ কিন্তু জাপানের সেই সময়ের ফ্যাসিবাদী চরিত্র ফুটিয়ে তোলে।
চীনের কথা বললে চিয়াং কাইয়ের শাসনের সময়কালে (১৯৩০-৪০) যে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শাসনের অনেক বৈশিষ্ট্য মিলে যায়। বিশেষ করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমন, একদলীয় শাসন এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।
আর উত্তর কোরিয়ার কিম পরিবারের পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকেও অনেক বিশ্লেষক ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মিশ্র রূপ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। পাকিস্তানে আয়ুব খান, জিয়াউল হকের মতো শাসকেরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। যদিও এই বৈশিষ্ট্যকে ‘ক্লাসিক্যাল ফ্যাসিবাদ’ বলা যায় না, তবে মিলিটারি ফ্যাসিজমের কিছু উপাদান সেখানে পাওয়া যায়।
অনেকেই ভাবেন, হিটলারের পতনের পর ফ্যাসিবাদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, ফ্যাসিবাদ তার রূপ পাল্টে, বিভিন্ন নামে ও মাধ্যমে এখনও টিকে আছে। আজকের দিনে যাকে ‘নব্য-ফ্যাসিবাদ’ (neo-fascism) বলা হয়, তা অনেক দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।
এখন প্রশ্ন আসতে পারে নব্য-ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য কি হিটলারের সময়কার ফ্যাসিবাদের চেয়ে ভিন্ন? মিলিয়ে দেখা যাক। মূলত নব্য-ফ্যাসিবাদের যে চিহ্ন তার মধ্যে অভিবাসীবিরোধী মনোভাব, ধর্মীয় ও জাতিগত ঘৃণা প্রদর্শন, গণমাধ্যমকে শত্রু বানিয়ে ফেলা, শাসকের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যে বাধ্য করা অন্যতম।
ইউরোপের কিছু দেশে (যেমন হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড) ও আমেরিকার কিছু রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অনলাইনে উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এবং ‘অল্ট-রাইট’ মতাদর্শের উত্থানও ফ্যাসিবাদী চিন্তাভাবনার আধুনিক রূপ।
এই যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের দেশের স্বার্থে দেশে দেশে শুল্ক বসিয়ে দিলেন, টালমাটাল করে তুললো গোটা বিশ্বের অর্থনীতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজের দেশকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন, অভিবাসীবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, ফিলিস্তিনে গাজায় ইসরায়েলের জাতিগত নিধন- এ সবই কিন্তু নব্য ফ্যাসিবাদের চিহ্ন ধারণ করে। তাহলে কি তারা ফ্যাসিবাদের ঊর্ধ্বে? প্রশ্ন উঠতে পারে ইরান, অথবা রাশিয়ার শাককদের নিয়েও।
তবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সবসময়ই বিভিন্ন স্তরের প্রতিরোধ দেখা গেছে। ইতিহাসে যেমন ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, তেমনি এখনো সমাজকর্মী, লেখক, শিক্ষাবিদ, এবং সাধারণ মানুষ এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেখান। ব্যাপক দমন-পীড়নের পরও ইরান, রাশিয়ার দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ফ্যাসিবাদ কালে কালে নানা রূপে ফিরে এসেছে। এমনও হয়েছে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে কোনো শাসককে অপসারণের পর দ্বিগুণ মাত্রার অন্য কোনো ফ্যাসিস্ট দখল করে নিয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা! বাংলাদেশের কথাই যদি বলি- ব্যাপক গণ আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হওয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেও ফ্যাসিবাদ অনুশীলনের অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী মত সহ্য করতে না পারা, তার দলের নেতাকর্মীদের একচ্ছত্র আধিপত্য, দমন-পীড়নে সরকারি বাহিনীর ব্যবহারের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়। আর এসব অভিযোগের বোঁঝা কাঁধে নিয়ে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে তাকে। শুধু ক্ষমতা নয়, দেশছাড়া করা হয়েছে সাবেক এই সরকার প্রধানকে। এরপরের মাসগুলোতে আমরা যে চিত্র দেখছি, বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে নৃশংসতার যে খবর উঠে আসছে প্রতিনিয়ত তা কি বিগত সরকারের চেয়ে কোনো অংশে কম বা ভিন্ন?
আদিবাসীদের অধিকার হরণ, বিরোধী মত দমন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে বর্তমান অন্তর্বর্তী শাসকের সময়েও। কেউ কেউ তো মুখ ফসকে বলেই ফেলছেন- আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে এ ধরনের প্রবণতা। তাহলে কি মুহাম্মদ ইউনূস হয়ে উঠছেন দক্ষিণ এশিয়ায় ফ্যাসিস্টের নতুন মুখ?
তবে এটি সত্যি, ফ্যাসিবাদ তখনই মাথা তুলে দাাঁড়ায় যখন মানুষ ভয়, বিভ্রান্তি ও হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আমাদের দায়িত্ব এই ভয়কে ভালোবাসায়, বিভক্তিকে সংহতিতে রূপান্তরিত করা। রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সকলের মাঝে সাম্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া গেলে ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পেতে পারে একটি রাষ্ট্র, একটি জাতি।
এহেছান লেনিন, সংবাদকর্মী ও গবেষক।