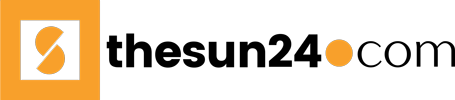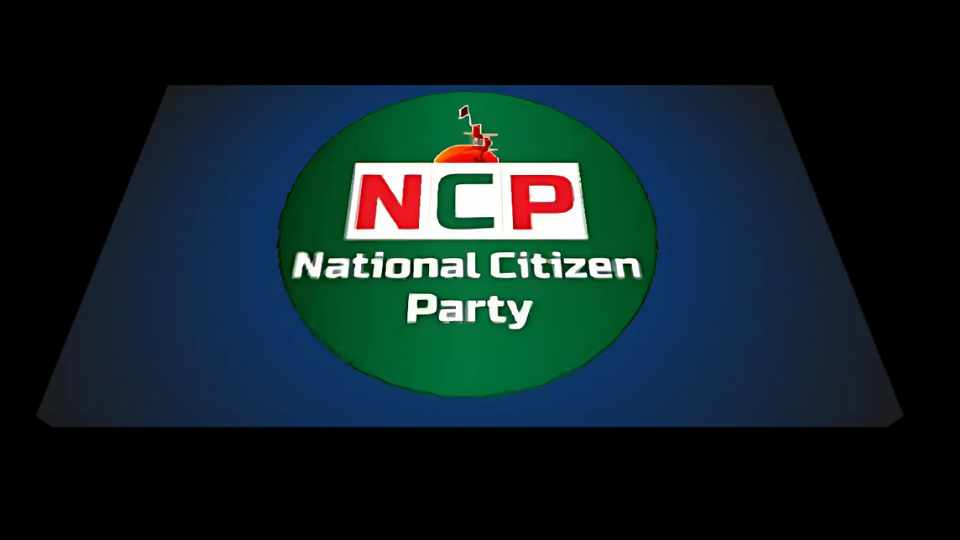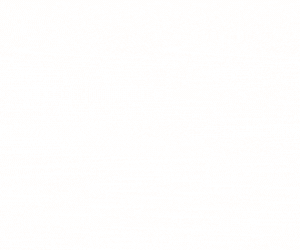খুব বেশি দিনের কথা না, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলোর ভাগ্য নির্ধারণ হতো সেনানিবাসে। রাতের আঁধারে জেনারেলদের গোপন বৈঠক, ভোরে রাজধানীতে ট্যাঙ্কের গর্জন, আর রেডিও সম্প্রচারে সামরিক শৃঙ্খলার ছাপমাখা “নতুন নির্দেশ” ছিল পরিচিত দৃশ্য।
ইসলামাবাদ থেকে ঢাকা, সব জায়গায় একই নাটক: ওয়াশিংটন বা মস্কোর তত্ত্বাবধানে অভ্যুত্থান, আর শীতল যুদ্ধের দাবায় উভয় পক্ষই বসাত মনের মতো ঘুঁটি।
সে যুগ শেষ। এখন এসেছে নতুন মডেল, যা মার্চপাস্ট করে না, বরং ট্রেন্ড হয়। ক্ষমতা পরিবর্তন এখন লাইভ-স্ট্রিমে দেখা যায়। হ্যাশট্যাগে ছড়িয়ে পড়ে, আর অ্যালগরিদমে গতি পায়। স্মার্টফোন হাতে তরুণ-তরুণীরা, বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীরা হয়ে ওঠে অগ্রণী।
তাদের ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে এমন প্ল্যাটফর্ম, যা মূলত দেখনদারিকেই প্রাধান্য দেয়, বিষয়বস্তুকে নয়। এক সময় নাটকের নায়ক সেনাবাহিনী এখন নেপথ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু তখনই এগিয়ে আসে, যখন জনআন্দোলনের ঢেউ প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
বিদেশি শক্তিগুলো আর জেনারেলদের অস্ত্র পাঠায় না। তারা এখন অর্থ ঢালে এনজিওতে, কর্মী ও প্রভাবশালীদের উজ্জীবিত করে, যারা মুহূর্তে ভাইরাল করে তুলতে পারে রাজনৈতিক বয়ান।
এটাই “সোশাল মিডিয়া অভ্যুত্থান”। বাহ্যিকভাবে অনেকটা পরিষ্কার, কম স্বৈরাচারী, এমনকি দেখতে গণতান্ত্রিকও। কিন্তু আড়ালে এর ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে অতীতের রূঢ় অভ্যুত্থানের চেয়েও গভীর।
দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র; শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তানে সরকার হেঁটেছে পতনের কিনারায়। কখনও ভেঙেও পড়েছে ডিজিটাল আন্দোলনের ভারে। এমনকি এই অঞ্চলের হাতি ভারতও পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারছে না সেই কম্পন।
এখন প্রশ্ন হলো; দক্ষিণ এশিয়া বাইরের উসকানিতে পরিবর্তনের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিজিটালি সাজানো বিদ্রোহগুলো কি কেবল বিশৃঙ্খলাই রেখে যায়?
শ্রীলঙ্কায় বংশ থেকে মিম
২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার রাজাপাকশে বংশের পতন এই নতুন যুগের প্রথম ভূমিকম্প হয়ে আসে।
অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলে কলম্বোর রাস্তায় জ্বালানি লাইনের দীর্ঘ সারি, জীবনের গতি থেমে যায়। আরাগালায়া (“সংগ্রাম”) আন্দোলন শুরু হয় মধ্যবিত্ত যুবকদের হাত ধরে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তা রূপ নেয় গণবিস্ফোরণে।

সোশাল মিডিয়া দিল গতি। গোতাবায়া রাজাপাকশের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সুইমিংপুলে বিক্ষোভকারীদের আরাম করে বসে থাকার ছবি ভাইরাল হলো গোটা বিশ্বে। জাতীয় সংকট পরিণত হলো মিম-চালিত নৈতিক নাটকে। প্রতীকী বার্তাটি ছিল ধ্বংসাত্মক: এক সময়ের অস্পৃশ্য রাজবংশ স্রেফ ভেঙে পড়ল ইন্টারনেটের কৌতুকে।
সেনাবাহিনী দমন না করে নিল সংযমের পথ। তারা নিজেদের উপস্থাপন করল জনশৃঙ্খলার অভিভাবক হিসেবে, নীরবে নিজেদের পাশ থেকে রাজাপাকশেদের সরিয়ে দিল। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আনুরা কুমারা দিসানায়েকে ও তার ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার জোট ক্ষমতায় আসে। বিদেশে এটিকে গণশক্তির বিজয় বলা হলো।
কিন্তু বাহ্যিক রূপের আড়ালে দেশ রয়ে গেল দেউলিয়া, ঋণদাতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের কাছে নির্ভরশীল। হ্যাশট্যাগ রাজবংশকে নামিয়েছে, কিন্তু শ্রীলঙ্কার আর্থিক পতন মেরামত করতে পারেনি।
অচলাবস্থায় বাংলাদেশের বিপ্লব
২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশও একই পথে হাঁটল।
যা শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন হিসেবে, তা দ্রুত রূপ নিল শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। ঢাকার রাস্তায় জ্বলে উঠল উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, আর ভাইরাল হলো পুলিশের সহিংসতার ছবি।
অশান্তি ছড়িয়ে পড়লে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস এলেন অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে। তার বৈশ্বিক খ্যাতি যেন দিল বাড়তি মর্যাদা। সোশাল মিডিয়া একে চিত্রিত করল নৈতিক কাহিনি হিসেবে। ইউনূসকে নোবেলজয়ী সংস্কারক ও এক শক্তিমান নারীশাসককে সাহসী ছাত্ররা জয় করছে এমনভাবে দেখানো শুরু হয়।

কিন্তু বাস্তবতা অনেক জটিল। এক বছর পার হয়ে গেছে, অন্তর্বর্তী সরকার অচল। কারখানা বন্ধ, বেকারত্ব বেড়েছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি নেমেছে চার দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।
ছাত্রনেতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে টেকনোক্র্যাটরা। ফেরত আসা রাজনৈতিক দলগুলো, কেউ কেউ ইসলামপন্থী কর্মসূচি নিয়ে ক্ষমতার ভাগীদার হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আর এসব উসকে দিচ্ছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার আশঙ্কা।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অস্থিরতাকে দেখানো হলো কেবল ভাইরাল ছবির ভেতর দিয়ে: পতাকা, ভাষণ, নির্বাসন। হারিয়ে গেল গভীরতর কাহিনী; অস্থিরতায় জর্জরিত এক অর্থনীতি, আর একটি দেশ, যা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত গণহত্যা থেকে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে।
সোশাল মিডিয়া সহজ করেছে বয়ানকে। কিন্তু শাসনব্যবস্থার ভাঙন জোড়া লাগাতে পারেনি।
হ্যাশট্যাগ ও অস্থিরতা: নেপালের অশান্ত অধ্যায়
নেপালের পালা আসে যখন সরকার ভিন্নমত দমন করতে ২৬টি সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্ম নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এই পদক্ষেপ ভয়াবহভাবে উল্টে যায়। তরুণদের ক্ষোভ রাস্তায় বিস্ফোরিত হয়, আর “#NepoKids” রাজনৈতিক অভিজাতদের সন্তানদের নিয়ে তির্যক একটি হ্যাশট্যাগ অবিরাম ট্রেন্ড হতে থাকে।

বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা অলি পদত্যাগ করেন। সেনাবাহিনী কারফিউ জারি করে শৃঙ্খলা ফেরায়। তবে নিজেদের উপস্থাপন করে স্থিতিশীলতার রক্ষক হিসেবে, উস্কানিদাতা হিসেবে নয়। ১৯ জন নিহত হলেও ভাঙন স্পষ্ট হয়ে ওঠে: এক প্রজন্ম পুরনো রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হয়ে পড়েছে।
তবে বিক্ষোভকারীদের দাবিগুলো নতুন ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়। দুর্নীতি ও সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছাড়াও উঠে আসে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার এবং নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর দাবি। যা শুরু হয়েছিল স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে ডিজিটাল বিদ্রোহ হিসেবে, এখন সেটি নেপালের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে পুনর্গঠনের ঝুঁকি তৈরি করছে।
পাকিস্তানে অপেক্ষার খেলা
পাকিস্তানে নাটকের পর্দা এখনও নামেনি। সেনাবাহিনী এখনও রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে, কঠোর হাতে দলগুলোকে প্রভাবিত করছে। তবু ক্ষোভ জিইয়ে আছে।
ইমরান খানের দলে নিষেধাজ্ঞা, বারবার হওয়া বেলুচ বিক্ষোভ, আর নতুন আধাসামরিক বাহিনী গঠনের ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রভাব নিয়ে শঙ্কিত।

এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ জেনারেলদের হাতেই। কিন্তু পাকিস্তানের বিপুল তরুণ জনসংখ্যা, যারা ডিজিটালি সংযুক্ত এবং প্রতিবেশীদের উদাহরণে উৎসাহিত, একদিন হয়তো দমননীতির সীমা পরীক্ষা করবে।
যখন সেই স্ফুলিঙ্গ জ্বলবে, তখন হয়তো সেনাবাহিনী আবার পিছু হটবে। জনগণের হাতে সরকার পতনের সুযোগ দিয়ে পরবর্তীতে চূড়ান্ত সালিশকারী হিসেবে নিজেদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করবে।
ভারতের জন্য অপেক্ষমাণ হাতি
বড় প্রশ্ন হলো, ভারতও কি একই ধরনের পরিণতির মুখে পড়তে পারে? ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলো, যদিও ত্রুটিপূর্ণ, তবু প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল।
অর্থনীতিও শক্তিশালী, যা তরুণ প্রজন্মের জন্য বেশি সুযোগ তৈরি করছে। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কও দেশটিকে বাইরের রাজনৈতিক প্রকৌশল থেকে কিছুটা সুরক্ষা দেয়।
তবে সুরক্ষা মানেই অনাক্রম্যতা নয়। ভারতের চরম বৈষম্য, উচ্চ বেকারত্ব, আর অভিজাত শ্রেণির দখল প্রতিবেশীদের মতোই পরিস্থিতি তৈরি করছে।
সোশাল মিডিয়া বিশাল জগৎ ভারতের ক্ষেত্রেও উর্বর ভূমি। সেখানে ডিজিটালি সংগঠিত অস্থিরতা সহজেই জন্ম নিতে পারে। কোনও বড় সংকট দেখা দিলে এর ব্যাপ্তি দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনও দেশের অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে।
বৈশ্বিক পাঠ
দক্ষিণ এশিয়ার ধারাবাহিকতা আসলে বৈশ্বিক কাহিনির প্রতিফলন।
শীতল যুদ্ধকালে যেখানে অভ্যুত্থান হতো পরাশক্তির অর্থায়নে, আর জেনারেলরা পেত অস্ত্র। সেখানে আজকের ক্ষমতার পালাবদল অনেক সূক্ষ্ম। কর্মী ও এনজিওরা পায় অর্থায়ন, প্রভাবশালীরা পায় প্রচার, আর সেনাবাহিনী দেরিতে হস্তক্ষেপ করে, যাতে আন্দোলনগুলো দেখতে “নাগরিক-নেতৃত্বাধীন” মনে হয়।
ইউটিউব, ফেইসবুক, এক্সের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো এখন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। নিরপেক্ষ হওয়ার দাবি থাকলেও তাদের অ্যালগরিদম আসলে সুবিধা দেয় ক্ষোভ আর দেখনদারিকে। দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষোভ নামিয়ে আনা হয় মিম আর হ্যাশট্যাগে।
প্রতিবাদী নেতারা হয়ে ওঠে প্রভাবশালী ইনফ্লুয়েন্সার। প্রতিদান হিসেবে তারা পান অনুসারী সংখ্যা, কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নয়। বিপ্লব রূপ নেয় ভাইরাল পণ্যে।
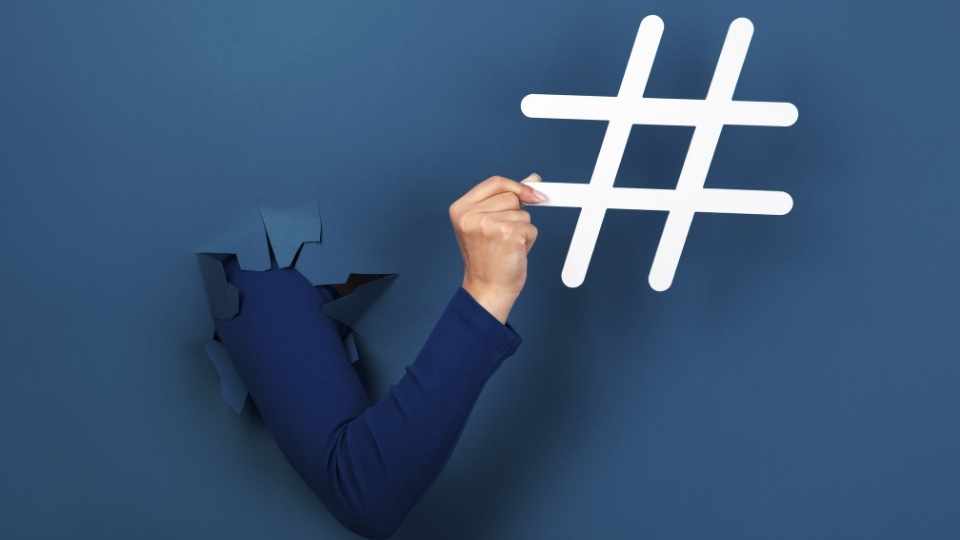
বিদেশি শক্তিগুলো এই গতিকে দক্ষভাবে কাজে লাগায়। কনটেন্ট নির্মাতা ও বয়ান-নেটওয়ার্কে অর্থ ঢেলে তারা গড়ে তোলে জনমত; খরচ কম, প্রভাব ব্যাপক।
অনেক তরুণ দক্ষিণ এশীয়র জন্য কনটেন্ট নির্মাণই হয়ে উঠছে জীবিকা, যা প্রায়ই অর্থায়ন করে দাতারা বা অজ্ঞাত পৃষ্ঠপোষকরা। ফলে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে একইসঙ্গে দেখনদারি ও পেশা।
ভোক্তা-পণ্য হিসেবে বিদ্রোহ
এখানেই লুকিয়ে আছে এক বৈপরীত্য। একসময় সমৃদ্ধির পথ বলে বিবেচিত পুঁজিবাদ এখন অস্থিরতাকেও বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে।
বিদ্রোহ বাজারজাত হচ্ছে ভোক্তা-পণ্যের মতো লোগো, হ্যাশট্যাগ, নায়োকোচিত চিত্রকল্পে প্যাকেজ করা। ক্ষোভ হয়ে উঠছে লাভজনক সম্পদ, যা সিলিকন ভ্যালি আহরণ করছে আর ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ব্যবহার করছে। এটি কোনও অর্থেই গণতন্ত্র নয়।
এটি আসলে রাজনৈতিক প্রকৌশল, যা সাজানো হয় গণশক্তির আবরণে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সীমিত সুযোগ পাওয়া তরুণ প্রজন্মকে খাওয়ানো হয় সরলীকৃত বয়ান, যা ক্ষোভ জাগায়, কিন্তু খুব কমই সমাধান দেয়।
তাদের আবেগ হয়ে ওঠে বৈশ্বিক পুঁজির যন্ত্রের কাঁচামাল। সরকার ভেঙে পড়ে, কিন্তু ঋণ, দুর্নীতি ও দুর্বল প্রতিষ্ঠান রয়ে যায় অক্ষত।
এক হ্যাশট্যাগ দূরে
দক্ষিণ এশিয়ার অস্থিরতা; শ্রীলঙ্কার মিম-বিপ্লব, বাংলাদেশের অনিশ্চিত উত্তরণ, নেপালের হ্যাশট্যাগ বিদ্রোহ কিংবা পাকিস্তানের জ্বলন্ত ক্ষোভ দেখাল, ‘অভ্যুত্থান এখন ডিজিটালে রূপান্তরিত’। ভারত হয়তো বেশি স্থিতিশীল, কিন্তু কোনও রাষ্ট্রই পুরোপুরি নিরাপদ নয়।
সরকারগুলোর জন্য শিক্ষা হলো; প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করলে হয়তো অস্থিরতা কিছুটা দেরি হয়। কিন্তু তরুণদের ক্ষোভকে উপেক্ষা করা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আর যুব আন্দোলনের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো; দৃশ্যমানতার দেখনদারিকে কীভাবে বাস্তব সংস্কারে রূপান্তর করা যায়।

বিশ্বের কাছে প্রশ্নটি রাজনৈতিক যেমন, তেমনি নৈতিকও। যখন পুঁজিবাদ ক্ষোভকে বাণিজ্যিক সম্পদে রূপ দেয়, আর কর্মী ও অ্যালগরিদমের হাতে আউটসোর্স করে ক্ষমতাপাল্টার প্রক্রিয়া, তখন অস্থিরতা কোনও ব্যবস্থার ত্রুটি নয়। এটাই হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসায়িক মডেল।
সবচেয়ে অস্বস্তিকর সত্য হলো; পরবর্তী বিপ্লব হয়তো পরিকল্পিত হবে না কোনও সেনানিবাসে বা বিতর্কিত হবে না কোনও সংসদে। এটি হয়তো কোডেড হবে কোনও অ্যালগরিদমে, রাখা থাকবে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের সার্ভারে, আর আসবে এক ট্রেন্ডিং হ্যাশট্যাগের গতিতে।
তথ্যসূত্র : এশিয়া টাইমস। লেখক ম্যাক খান একজন উন্নয়নকর্মী। তিনি জাতিসংঘের সাবেক আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট ও মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির সাবেক একাডেমিক।